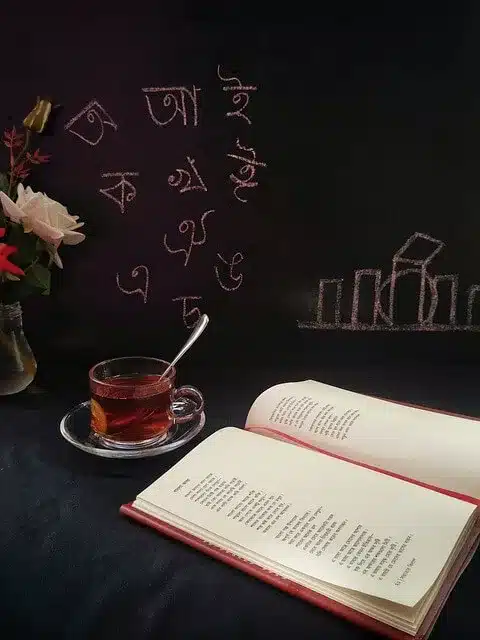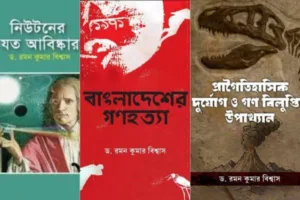একুশে ফেব্রুয়ারি রচনাঃ ভাষা আন্দোলন কি
ভূমিকা: একুশে ফেব্রুয়ারি রচনা লিখতে গেলে কি কি লিখতে হয়?
নিচের লেখাটি মূলত যারা স্কুল বা কলেজে একুশে ফেব্রুয়ারি রচনা লিখতে চায় তাদের কথা মাথায় রেখে লেখা হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি অনুচ্ছেদ মূলত ১০টি বাক্য হলেই যথেষ্ট তবে কেউ চাইলে বেশি লিখতে পারে। যেহেতু আমি ভাষা আন্দোলন কি এবং এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও লিখছি। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি রচনা লিখতে গেলে মুল বিষয় লিখলেই হয়।
একুশে ফেব্রুয়ারি, বাংলার ইতিহাসে একটি অম্লান দিন। ১৯৫২ সালের এই দিনে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য পাকিস্তানি সরকারের নির্মম গুলির শিকার হয়েছিলেন বহু নিরপরাধ ছাত্র। তাদের আত্মত্যাগের স্মরণে আমরা প্রতি বছর এই দিনটি পালন করি ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে।
বর্তমানে দেখছি একুশে ফেব্রুয়ারি রচনা লিখেতে বলা হলে ছাত্রছাত্রীরা খুঁজে পায়না কি লিখবে । মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস আর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের সাথে গুলিয়ে ফেলে। যারা একুশে ফেব্রুয়ারি রচনা লিখবে তারা কয়েকটি বিষয় মনে রাখবে
একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে ১০টি বাক্য লিখলেই হবেঃ
একুশে ফেব্রুয়ারি রচনা কিকি থাকবে
১। ঘটনার তারিখঃ
২। ঘটনার বিবরণঃ
৩। ঘটনার প্রেক্ষাপটঃ
৪। রাজনৈতিক অবস্থাঃ
৫। ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য
৬। ভাষা আন্দোলনে কে কে শহীদ হয়েছিল
৭। কিভাবে বাংলাদেশ স্মরণ করে দিনটি
৮। কিভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ স্মরণ করে দিনটিকে ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে
৯। আমাদের কি করা কর্তব্য
১০। বাংলা ভাষা রক্ষায় একুশে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব ও আমাদের করনীয়
এই ১০টি বাক্যের উত্তর লিখলেই একুশে ফেব্রুয়ারি রচনা সুন্দর ভাবে লেখা হবে। তবে এটা একটা সাজেশন মাত্র। যে কেউ আরও সুন্দর করে লিখতে পারে।
ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট:
(একুশে ফেব্রুয়ারি রচনা লিখেতে গিয়ে এই অংশটি যদি খুব বেশি প্রয়োজন না হয় তবে এড়িয়ে গেলেও হবে)
১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে পাকিস্তানি সরকার। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়।
আমরা হয়তো অনেকেই জানিনা ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্ব ছাড়াও বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ছিল। ঠিক যে কারণে বৃটিশদের কাছ থেকে ভারত পাকিস্তান আলাদা হয়েছিল সেই ধর্মীয় দ্বন্দ্বের থেকেও অন্য ছোট ছোট মানসিক ও সামাজিক বৈষম্য একেবারে অবজ্ঞা করা যায় না। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে যখন আমি কিছু বই পত্র পড়া শুরু করলাম তখন।
একটি বই আমাকে খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করল ইংরেজিতে লেখা সেই বইয়ের কিছু বিষয় নিয়েই আজকের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গুটি কয়েক ঐতিহাসিক সত্যতা ভিত্তিতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ভারত পাকিস্তান দ্বন্দ্বের মধ্যে ধর্মীয় কারণটাই প্রধানত ছিল মূল।
একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালের যে দাঙ্গা হয়েছিল পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর পালিত প্রশাসনিক বাহিনী নির্বিচারে গুলি করেছিল ভাষা আন্দোলনের মিছিলে কিন্তু কেন ভারত পাকিস্তানের যে যে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব সেটাতো অবসান হওয়ার কথা কারণ পাকিস্তানের দুটি প্রদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে রচিত সেই মুসলিম ভাইয়ে ভাইয়ে কেন দ্বন্দ্ব শুরু হল আবার ভারত পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার পরে পূর্ব পাকিস্তানের কি এমন ঘটেছিল যাতে ভাইয়ে ভাইয়ে আবার দ্বন্দ্ব শুরু হল কারণ জানতে হলে দ্বন্দ্বের মৌলিক বিষয়গুলো শোষক ও শোষিত শ্রেণির মধ্যে, জমিদার ও কৃষকের মধ্যে, পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের মধ্যে বিশদভাবে জানা দরকার। জাতিগত, আঞ্চলিক, ভাষাগত এবং সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের মতো আরও কিছু ছিল যা ব্রিটিশ-ভারতীয় শাসনের পরেও চলমান ছিল।
ভারতীয় জনগণ এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত ভাগের সাথে দূর হয়ে যায়, যদিও সাম্প্রদায়িকতা তখনো দুটি দেশের মধ্যে বেশ শক্তিশালীভাবে টিকে ছিল।
পূর্ব বাংলায়, বর্ণ হিন্দুরা সমাজে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বর্ণ হিন্দু বলতে বোঝায় উচ্চবর্ণের তথাকথিত হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ করে ব্রাহ্মণ অথবা সাহা অথবা জমিদার শ্রেণীর হিন্দু বণিকদের বোঝানো হয় যারা অঢেল অর্থ সম্পদের মালিক । বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্ত হিন্দুদের আধিপত্য প্রায় রাতারাতি শেষ হয়ে যায়। প্রথম কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কাছে চলে গিয়েছিল এবং দ্বিতীয় কারণ বর্ণহিন্দুরা অবিশ্বাস্যভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভারতে পাড়ি দিয়েছিল।
এর অর্থ হল জমির মালিকানা এবং মহাজন আর হিন্দুদের হাতে নেই। নিম্ন বর্ণের জনসাধারণ ও খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক অটুট ছিল, কিন্তু জমিদার এবং সুদগ্রহীতার সাম্প্রদায়িক চরিত্র বদল হয়েছিল কারণ উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ভারতে চলে যাওয়ার কারণে তাদের ব্যবসা অথবা আর্থিক বিষয়াদি মুসলমানদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে হয়েছিল। ইসলামে সুদে টাকা ধার দেওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু ধর্মের নির্দেশ মেনে চলার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য কৃষকদের ঋণের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে, গ্রামীণ মহাজনীকরণের কাজটি মুসলমানদের হাতে নেওয়া হয়েছিল।
গ্রামীণ অর্থঋণ ব্যবস্থা ছিল একটি স্বতন্ত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এবং এটি সাধারণত প্রথাগত জমিদার বা হিন্দু মহাজন দ্বারা পরিচালিত হতো না। হিন্দুদের বিশেষ গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হতো। সেই বিশেষ জাতি ‘সাহা’ দের প্রস্থানের সাথে সাথে সেই প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে যায় এবং অর্থঋণ ব্যবস্থাটি পরিচালনা করা মুসলমান জমিদার বা জোতদারদের একটি কাজে পরিণত হয়। তারা পুরানো প্রথাগত জমিদার ছিল না, কিন্তু তারা জমির মালিক শ্রেণী হিসাবে তাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলুপ্তির সাথে, এই জমিদার-সহ-মহাজনকারীরা উভয়ের কাজগুলিকে একত্রিত করেছিল। এইভাবে জোতদার-মহাজন বা জমিদার-মহাজনরা দেশভাগ-পরবর্তী পূর্ব বাংলায় নতুন গ্রামীণ প্রভু হিসেবে আবির্ভূত হয়।
এর ফলশ্রুতিতে, মুসলিম কৃষক, দরিদ্র কৃষক এবং ভাগচাষী এবং গ্রামীণ মজুরি-শ্রমিক, জমিদার এবং সুদগ্রহীতা গণ একই সাথে ওঠাবসা চলাফেরা করতে শুরু করতে বাধ্য হয়েছিল। একই অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে নিজেদেরকে খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু অতীতের থেকে পার্থক্য শুধু একটাই তারা এখন আর হিন্দু মুসলিম এই দুই ভাগে বিভক্ত নয় তারা এখন একই সম্প্রদায় ভুক্ত তা হল ইসলাম ও মুসলিম ভাতৃত্ব।
এই পরিবর্তন শুধু গ্রামাঞ্চলে এবং কৃষিক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং উৎপাদন ও বণ্টনের সকল ক্ষেত্রে, শিল্প ও ব্যবসায় এবং বিভিন্ন পেশায় ঘটেছে। মুসলিম কৃষক, শ্রমিক, কারিগর এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ তাদের সম্পত্তির সাথে একই সম্পর্কের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু এই ধরনের সম্পর্কের আর কোন সাম্প্রদায়িক মাত্রা ছিল না। শোষক এবং শোষিতরা এখন গ্রামীণ এলাকায় উন্মুক্তভাবে এবং কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই অকপটে একে অপরের মুখোমুখি হয়।
মুসলমানদের মধ্যে প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণি একটি বিষয় দেখতে পেল যে, আশেপাশে এমন কোনো হিন্দু নেই যাকে তাদের শোষক ও নির্যাতনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পরিবর্তে, তারা দেখতে পেল যে অবাঙালি মুসলমানরা আমলাতান্ত্রিক সরকারী কর্মকর্তা, ব্যবসা এবং যেকোন শিল্প কারখানা নিয়ন্ত্রণ করত এবং শাসক দলের বাঙালি রাজনীতিকরা পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সেবক ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি।
ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তরঃ খাজা নাজিমুদ্দিন
এইভাবে সমগ্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়, এবং যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের কারণে দেশ ভাগ হয়েছিল, তা পুনরায় চেপে বসেছিল একই দেশের দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের একই মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক কালচার এবং দর্শনের ভিত্তি তে এই অশান্তোষ আরো বেশি দানা বেঁধেছিল।
মুসলিম কৃষক, শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত জনগণকে ব্রিটিশ হটাও আন্দোলনে মুসলিম লীগ পাকিস্তানকে মুসলিমদের জন্য একটি স্বপ্নভূমি হিসাবে কল্পনা করতে শেখানো হয়েছিল, যেখানে দুধ এবং মধু অবিরাম প্রবাহিত হবে, সুখের নদী প্রবাহিত থাকবে , প্রত্যেকে শিক্ষা এবং উপযুক্ত চাকরি পাবে, স্বাস্থ্যসেবা একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। একটি সুস্থ ইসলামিক সংস্কৃতির ফুল ফোটানো হবে যার জন্য পাকিস্তান আন্দোলনের সময় জনসাধারণকে বলা হয়েছিল এবং প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।
পূর্ব বাংলার মুসলমানরা, যারা জনসংখ্যার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তারা পাকিস্তান নামক স্বপ্নভূমির অনুর্বরতা দেখে বেশ বিভ্রান্ত ও হতবাক ছিল, যেখানে তাদের ক্ষুধার্ত এবং দুর্ভিক্ষে মরতে হয়েছিল, যেখানে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে কোন উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হয়নি। ভাগচাষিরা, যেখানে শ্রমজীবী জনগণ এবং জনগণের শিক্ষিত অংশের জন্য নতুন সুযোগ উন্মুক্ত হয়নি এবং সমস্ত ক্ষেত্রে জীবন আগের মতোই দুর্বিষহ ছিল।
ব্রিটিশ-ভারতে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে মুসলিম লীগ মুসলমানদের শিখিয়েছিল ব্রিটিশ ও হিন্দুদের শত্রু মনে করতে। ভারত ও বাংলার স্বাধীনতা এবং বিভক্তির সাথে সাথে, উভয়েই আবির্ভূত হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক অবাঙালিরা, বেশিরভাগই পাঞ্জাবি, শত্রুর কাতারে তাদের উপস্থিতি তৈরি করে।
এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে, পুরানো ধরণের একটি ভুল ক্রমবর্ধমানভাবে মানুষ আঁকড়ে ধরতে থাকে আর সেটা হল বর্ণহিন্দুরাই ছিল বৃটিশ-ভারতে বাংলার কৃষকদের নিপীড়ক । পরবর্তীতে মুসলমান কৃষকরা ভেবেছিল যে তারা হিন্দুদের দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। যদি বর্ণ হিন্দুরা ইতিমধ্যেই ভারতে পাড়ি দিয়েছে। মুসলমানরা তখনও এই ধরনা পোষণ করতো যে তারা যে শোষিত হচ্ছে তা মূলত হিন্দুরাই করছে যদিও এর কোন যুক্তি খাটে না কারণ ইতিমধ্যেই হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্থান ত্যাগ করেছে।
এমন পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্থান থেকে মুসলিম লীগ বাংলার মুসলিম কৃষকদের মনে এই বিভ্রান্তি ব্যবহার করেছিল এবং সঠিক রাজনৈতিক প্রচারের অভাবে মুসলিম কৃষকরা মনে করেছিল জমিদার এবং মহাজনরা রাই এর নেপথ্যে রয়েছে। যদিও প্রকৃত বর্ণ হিন্দু মহাজন রা তখন অনুপস্থিত। তবে এমন মনে করার কারণ আসলে পাঞ্জাবি অ-বাঙালি মুসলিমগন যে নেপথ্যে নিপীড়ন করছে তা ছিল অন্তরালে তাই এদেশের মুসলমান গন হিন্দুদেরকেই তখন মনে মনে দায়ী করতো।
অর্থনৈতিক জীবন এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। বেশিরভাগ ব্যবসা ও শিল্পের মালিকানা ছিল হিন্দুদের এবং বিভিন্ন পেশার অধিকাংশ লোকও ছিল হিন্দু। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল এবং বেশিরভাগ সংবাদপত্র তাদের মালিকানাধীন ছিল। এভাবে মুসলিম কৃষকদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি বিরাজ করছিল, সেই একই ধরনের বিভ্রান্তি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেও ধরা পড়ে এবং পরবর্তীদের মধ্যে সেই বিভ্রান্তি থেকে একই রাজনৈতিক ভুলের উদ্ভব হয়।
একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা: ভাষা আন্দোলন কি
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অংশ হিসেবে মিছিল শুরু করে। পুলিশ নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলি চালায়। রহিম, বরকত, সালাম, জব্বারসহ বহু ছাত্র শহীদ হন।
ভাষা আন্দোলনের প্রভাব:
ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভিত্তি স্থাপন করে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা তাদের ঐক্য ও সংহতির প্রমাণ দিয়েছিল।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র (১ম খণ্ড- ১৫তম খণ্ড)
একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য:
একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু একটি দিন নয়, এটি একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস । সারা বিশ্বের মানুষ এই দিনে মাতৃভাষাকে স্মরণ করে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে । বাংলাদেশে এই দিনে খালি পায়ে শহিদ মিনারে গিয়ে ফুল দেয়া হয় । শ্রদ্ধা জানানো হয় সমস্ত ভাষা শহীদের। এটি আমাদের মাতৃভাষা প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রতীক। এই ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে বাংলা একাডেমী সারা মাস ব্যাপী বই মেলার আয়োজন করে। ১৯৭২ সালে এই বই মেলা প্রথম শুরু হয়েছিল। একুশে ফেব্রুয়ারি রচনা প্রতিযোগিতা স্কুল কলেজ বা বিশ্ব বিদ্যালয়ে বা চাকুরীর পরীক্ষাতে লিখতে বলা হয়। তাই উপরোক্ত ১০টি প্রশ্নের উত্তর লিখলেই সুন্দর একটি মান সম্মত লেখা হবে বে আমার বিশ্বাস।
উপসংহার:
আমাদের সকলের উচিত ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের স্মরণে তাদের আদর্শ ধারণ করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা করা।